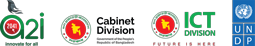তারিখ: ৭ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৪ উপলক্ষে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ঢাকা আয়োজিত সেমিনারের সেমিনার পেপার
বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের সমস্যা ও সম্ভাবনা
জয়দীপ দে
সি. ভি. গুড (C.V. Good) তাঁর Dictionary of education-এ লিখেছেন, All formal and informal activities and experiences that help to qualify a person to assume the responsibilities as a member of the educational profession or to discharge his responsibilities more effectively.
অর্থ দাঁড়ায়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ হচ্ছে সমস্ত প্রথাগত ও অপ্রথাগত কাজ ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়, যা একজন ব্যক্তিকে শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত হতে এবং তা অত্যন্ত কার্যকরভাবে পালন করতে যোগ্য করে তোলে।
তবে শিক্ষকদের শিক্ষাদান এখন আর প্রশিক্ষণের সংকীর্ণ ধারণায় আবদ্ধ নেই। তাই এখন আর শিক্ষক প্রশিক্ষণ না বলে শিক্ষক শিক্ষণ বলা হয়। তাই এশিয়ার অনেক পুরনো টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ইনিস্টিটিউট অব এডুকেশন অথবা কলেজ অব এডুকেশনে রূপান্তরিত হয়েছে।
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন সিঙ্গাপুরের একসময়কার পরিচালক মি. লি সিং কং-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সিঙ্গাপুর সরকার শিক্ষক প্রশিক্ষণকে কেমন গুরুত্ব দেয়?
উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সিঙ্গাপুরের এক টুকরো জমির দাম যেখানে হিরা জহরতের সমান, সেখানে শিক্ষক প্রশিক্ষণের এই ইনস্টিটিউটের জন্য সরকার ১৬ হেক্টর জমি দিয়েছে। এখানে লেখাপড়ার সুযোগ পাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার। এখানে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারলে একজন শিক্ষার্থীর সামাজিক মূল্যায়ন অনেক বেড়ে যায়। আর চান্স পেলেই উচ্চ বেতনের নিশ্চিত একটি চাকরি। সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা।
বাংলাদেশে ১১৫ বছর ধরে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ দীর্ঘ পরিক্রমায় অনেক সমস্যা ও সম্ভাবনা উঁকি দিয়েছে। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক সমাজ গড়ে তোলার জন্য এই কার্যক্রম পুনর্মূল্যায়নের দাবি রাখে।
পেছন ফিরে দেখা
উপমহাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল হচ্ছে ১৮৫৪ সালের উড ডেসপ্যাচ। সেখানে ভারতের প্রতিটি প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তথা নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি দেবার সুপারিশ করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত এই সুপারিশের বাস্তবায়ন হয়েছিল খুবই সামান্য।
১৮৫৯ সালের স্ট্যানলি ডেসপ্যাচও শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। বিদ্যমান শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়গুলোর মান নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। একই সঙ্গে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতনের জন্য স্কুলকে অনুদান প্রদানের প্রস্তাব করা হয়।
১৮৮১-৮২ সালে ভারতবর্ষে নর্মাল স্কুল ছিল ১০৬টি। এর মধ্যে ১৫ টি ছিল নারীদের জন্য। এখানে শিক্ষার্থী শিক্ষক ছিলেন ৩,৮৮৬ জন এবং বার্ষিক খরচ ছিল প্রায় চার লাখ টাকা। তবে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি ছিল কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য। এখানে ভর্তির যোগ্যতা ছিল প্রাথমিক উত্তীর্ণ হওয়া। কিন্তু মাধ্যমিকের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এসময় মাদ্রাজ ও লাহোরের নর্মাল স্কুলকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উপযুক্ত করা হয়।
১৮৮২ সালের হান্টার কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য পৃথক টিচার্স ট্রেনিং স্কুল স্থাপনের সুপারিশ করে। এর আলোকে ১৮৮৬ সালে মাদ্রাজ ও ১৮৮৯ সালে নাগপুরে ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।
উনবিংশ শতকের শেষের দিকে ভারতবর্ষে ছয়টি ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া। এগুলো হলো- মাদ্রাজ, লাহোর, রাজামুদ্রি, কার্শিয়াং, জব্বলপুর ও এলাহাবাদে। এর মধ্যে একটি বাংলা প্রদেশে। কার্শিয়ান টিচার্স ট্রেনিং কলেজ। কিন্তু কার্শিয়াং টিচার্স ট্রেনিং কলেজ শুরুতেই হোঁচট খায়। তিন বছরের (১৯০৩) মাথায় বন্ধ হয়ে যায়। তখন বাংলা প্রদেশে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাভ ৯২ হাজার। আর শিক্ষক সংখ্যা ৯ হাজার। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য তৎকালীন জনশিক্ষা বিভাগের প্রধান আলেকজেন্ডার প্যাডলার কলকাতায় এক কনফারেন্স ডাকেন। এই কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়-
১. উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রিটিশ শিক্ষকের নেতৃত্বে অন্তত ৩ টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ স্থাপন করা;
২. এক বছরের কোর্স পরিচালনা করা;
৩. জুনিয়র শিক্ষকরা এফএ এবং সিনিয়র শিক্ষকরা বিএ পাস করে এখানে ভর্তি করা;
৪. ভার্নাকুলার শিক্ষকদের কোর্স ৩ বছর থেকে কমিয়ে ১ বছর করা হবে।
এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১৯০৮ সালে কলকাতা ও পাটনায় এবং পরের বছর ঢাকায় টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরে সাধারণত দুধরনের প্রশিক্ষণ হয়: প্রি-সার্ভিস ও ইন সার্ভিস। প্রি-সার্ভিস প্রশিক্ষণ মূলত বিএড ডিগ্রিকে বলা হয়। আদর্শ পরিস্থিতিতে একজন শিক্ষক বিএড প্রশিক্ষণের পর বিদ্যালয়ে যাবেন। কিন্তু আমাদের দেশে তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা হয় না। ১৯৯২ সালের আগে বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেবল সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে পরিচালিত হত। তখন প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিয়ে সুধীমহলের প্রশংসা শোনা যেত। তবে বিশাল জনগোষ্ঠীকে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়েছিল আসন স্বল্পতার কারণে। ১৯৯২ সালে জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর মূলধারার এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রশিক্ষণার্থী স্বল্পতায় পড়ে। এখনো এ ধারা অব্যাহত আছে। বর্তমানে সরকারি ১৪ টি এবং বেসরকারি (অনুমোদিত) ৭৬ টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিএড) কোর্স চালু আছে। অনেক কলেজে মাস্টার্স অব এডুকেশন (এমএড) কোর্সও চালু রয়েছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ১৮ টি কেন্দ্রের মাধ্যমে বিএড কোর্স পরিচালনা করে। এছাড়া দেশের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা অনুষদে বিএড অনার্স কোর্স করানো হয়। সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতেও অনুরূপ কোর্স চালু আছে।
সমস্যা
পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো মূলত তিন ধরনের ভূমিকা পালন করে-
১. একাডেমিক
২. গবেষণা ও উন্নয়ন
৩. প্রশিক্ষণ বিস্তরণ
বর্তমানে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সমস্যা এই তিন ক্ষেত্রে আলোকপাতের দাবি রাখে।
একাডেমিক: টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মূলধারা হিসেবে পরিচিতি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও উপযুক্ত শিক্ষক নিয়ে শিক্ষার্থী পাচ্ছে না। ব্যানবেইসের ২০২২ সালের তথ্য মতে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে ২,৯৭৬ জন প্রশিক্ষণার্থী ছিল। যেখানে এই কলেজগুলোর আসন সংখ্যা ৭ হাজার ২০০ টি। অর্থাৎ ৬৯ শতাংশ আসন শূন্য ছিল।
কেন এই ভর্তি ক্ষরা? ১৯৯২ সালে জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে। সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে কম বেশি ১৬০ টি কর্মদিবস শ্রেণি কার্যক্রমে পরিচালিত হয়। এর মধ্যে ৭৫ শতাংশের কম উপস্থিতি থাকলে একজন প্রশিক্ষণার্থীকে চূড়ান্ত পরীক্ষা অংশ নিতে দেওয়া হয় না। সেখানে উন্মুক্ত বিশ্বিবদ্যালয়ে মাত্র ২৮ দিন শ্রেণি কার্যক্রমে পরিচালিত হয়। বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শ্রেণি কার্যক্রম আদৌ পরিচালিত হয় কীনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। কারণ এদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ-এর কোনো ব্যবস্থা নেই। অথচ বিএডের অর্ধক নম্বর অভ্যন্তরীণভাবে দেওয়া হয়। কিন্তু এই তিন উৎস থেকে প্রাপ্ত সনদের মান সমান। তাই শিক্ষার্থীরা সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হতে অনাগ্রহ বোধ করছে।
ছবি: Number of Institution, Teachers and Enrolment in Teacher Education by Type, Gender and Management 2022, BANBEIS.
একাডেমিশিয়ান ও প্র্যাকটিশিয়ানের মেলবন্ধন টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোর অনেক পুরনো সংস্কৃতি। টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ঢাকার প্রতিষ্ঠা লগ্নে ল্যাবরেটরি স্কুলের (আরমানিটোলা স্কুল) শিক্ষকগণ ক্লাস পরিচালনায় অংশ নিতেন। একইভাবে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষকগণ পরীক্ষামূলক ক্লাস নিতে স্কুলগুলোতে। এই সংস্কৃতি থেকে সরে আসায় টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোর প্রশিক্ষণের মান নিম্নগামী হয়েছে। এই মেলবন্ধন পুনঃস্থাপন জরুরি।
গবেষণা ও উন্নয়ন: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষার নীতিনির্ধারণী গবেষণা, শিক্ষা উপকরণ ও সামগ্রী তৈরিতে টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু বাংলাদেশে সেটা অনুপস্থিত দেখা যায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রতিনিধিত্ব থাকে আনুষ্ঠানিকতার অংশ হিসেবে। এসব প্রতিষ্ঠানের সঠিক দক্ষ ব্যক্তি নির্বাচন অথবা সৃজন এবং এর ব্যবহার দেখা যায় না।
টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমে অংশ না নেয়ায় একপাক্ষিক গ্রহীতায় (ইনটেকার) পরিণত হয়েছে। এতে করে কলেজগুলোর সামর্থ্যের পূর্ণ ব্যহার নিশ্চিত হচ্ছে না। বিদেশী অথবা বহুচর্চিত ধারণাগুলোই যুগের পর যুগ চর্চা করে যাচ্ছে। এসবের স্থানিক উপযোগিতা বিচার অথবা অভিযোজনায়ন হচ্ছে না একেবারে।
প্রশিক্ষণ বিস্তরণ: শিক্ষায় যুক্ত হওয়া নতুন নতুন ধারণা, জ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে শিক্ষকদের পরিচিত করতে ধারাবাহিক পেশাকালীন প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। আমাদের দেশেও ইন-সার্ভিস বা পেশাকালীন প্রশিক্ষণ হয়। কিছুদিন আগেও দফায় দফায় দেশজুড়ে শিক্ষকদের জাতীয় শিক্ষাক্রমের উপর প্রশিক্ষণ হয়েছে। কিন্তু এর ফলাফল খুব একটা সুখপ্রদ না। ০৬ জুলাই ২০২৪, দৈনিক প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘নতুন পদ্ধতির প্রশ্নপত্র শিক্ষকদেরই অনেকে বুঝছেন না, শিক্ষার্থীরা বিপাকে’। ১২ নভেম্বর ২০২৩ দৈনিক যুগান্তর রিপোর্ট করে, ‘নতুন শিক্ষাক্রম বুঝতে হিমশিম শিক্ষকদের।’
অর্থাৎ এ প্রশিক্ষণ খুব একটা কার্যকর হয়নি।
এর আগে সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতির উপর দেশব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। ২০১৭ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর পরিচালিত জরিপে দেখা যায় ৫২ শতাংশ শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতিই বোঝেন না। অবশ্য এর সঙ্গে আরেকটি তথ্য হলো মোট শিক্ষকের ৫৬ শতাংশ এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। অর্থাৎ ৪৪ শতাংশ কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই পাঠদান করেছেন এতোদিন।
ফলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ যেমন অপ্রতুল, তেমনি কার্যকরও নয়।
এর মূল কারণ আমাদের দেশে শিক্ষকদের ইন সার্ভিস ট্রেনিং কোনো নিয়মিত কার্যক্রম নয়। প্রকল্পভিত্তিক। প্রকল্পগুলোতে যারা পদায়ন পান তাদের মাধ্যমিক স্তর ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তেমন কোনো পূর্ব ধারণা থাকে না। প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত ম্যানুয়াল ও উপকরণ প্রণয়ন করে একেক সময় একেক সংস্থা। সেখানে কখনো প্রশিক্ষণ সম্পর্কে ধারণা সম্পন্ন ব্যক্তিরা থাকেন, কখনো থাকেন না। এই হযবরল অবস্থার জন্য এ দেশে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয় না।
সম্ভাবনা
শিক্ষক প্রশিক্ষণের পেছনে সরকারি বেসরকারি বিনিয়োগকে আমরা একটি সুসংবদ্ধ ধারায় প্রবাহিত করতে পারছি না। এর প্রধান কারণ এ নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ করার জন্য মাধ্যমিক স্তরে কোনো বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান এ দেশে নেই। অবশ্য প্রাথমিক স্তরে আছে।
ভারত পঞ্চাশের দশকে এই বাস্তবতা অনুভব করেছিল। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা- N.C.E.R.T (National Council of Educational Research and Training) প্রতিষ্ঠা করে। তারা শিক্ষক প্রশিক্ষণকে স্থায়ীরূপ দিতে ৪৩০টি DIET (District Institute of Education and Training) প্রতিষ্ঠা করেছে। এটিকে জেলাস্তরে মাধ্যমিক শিক্ষার শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষাসংক্রান্ত প্রি-সার্ভিস ও ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণ কার্যসূচির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এছাড়া তারা কিছু টিচার্স ট্রেনিং কলেজকে CTE (College of Teacher Education) এবং IASE (Institute of Advanced Studies in Education)-তে উন্নীত করে। সেগুলিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবনের।
এশিয়ান ডেভলাপমেন্ট ব্যাংকের অর্থায়নে নেক্সটজেন নামের একটি প্রকল্প সরকার হাতে নিতে যাচ্ছে। সেখানে ৪৫ টি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (টিটিআই) হবে। কিন্তু জাতীয় পর্যায় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান না থাকলে টিটিআইগুলো কার্যকর হবে না।
আমাদের একটি National Council of Educational Research and Training প্রতিষ্ঠা খুব জরুরি। এই প্রতিষ্ঠানটি পরিবীক্ষণের জন্য একটা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করবে। টিটিআই ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসগুলো দিয়ে পরিবীক্ষণ কার্যকর করবে।
উপসংহার
সম্প্রতি শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষক নিগ্রহ আমাদের শিক্ষকদের গ্রহণযোগ্যতা ও তাঁদের পেশাগত দক্ষতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। আজ থেকে ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে যে পেশাদারিত্ব দেখাতেন এখন সেটা দেখাচ্ছেন না বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এর পেছনে অনেকগুলো প্রপঞ্চ ক্রিয়াশীল হতে পারে। তবে আমার ধারণা, এর মধ্যে একটি হতে পারে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মানের অবনতি। এটি কোনো পরিবীক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই চলছে। এর ফলে শিক্ষকরা হয়ত সনদ পাচ্ছেন, কিন্তু গুণগত প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন না। তাই জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিকদের দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য এখনই শিক্ষক প্রশিক্ষণে যথাযথ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রের চাহিদাকে সামনে রেখে শিক্ষক প্রশিক্ষণের দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি গ্রহণ জরুরি।
.
জয়দীপ দে
সহকারী অধ্যাপক, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা
সেল: ০১৭২৭-৭৭৭৯৪৪, মেইল: joydip_dey@yahoo.com
(ইমেইলে চাহিত সূত্র সরবরাহ করা হবে)